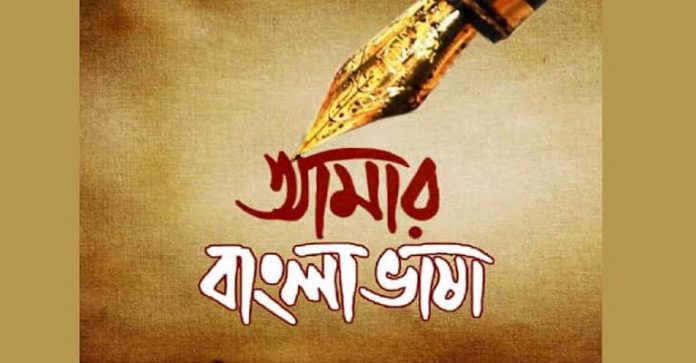আমাদের মাতৃভাষা বাংলা (bangla or bengali Language)। আমরা বাঙ্গালি। ভাষাকে অবলম্বন করেই এক একটি ভাষা সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে তাদের নিজের আচার ব্যবহার–কৃষ্টি–সংস্কৃতি–সাহিত্য–এক কথায় তাদের সভ্যতা। মন আছে বলেই মানুষ মননশীল। তার ভাব ও ভাবনার বিচিত্রতা মননশীল অনুভব ও বোধের মধ্য দিয়ে ক্রমাভিব্যক্তির পথে জন্ম দেয় ভাষা। বাংলাভাষার উদ্ভব ও তার বিকাশ জানতে গেলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে ‘ভাষা‘ কী? মানব মনের বিবিধ ভাবপ্রকাশের তাগিদ থেকেই ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ‘ এ ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে— ‘মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্পন্ন, বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে সুপ্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।‘
বাংলা ভাষার মূল উৎস হলো সংস্কৃতভাষা। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে ইন্দো–ইউরোপীয় ভাষা গোত্রে বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বাংলা ভাষাবিদদের মতে সংস্কৃতভাষা–সহ প্রাকৃত, অর্ধমাগধী ও পালির মতো ভাষা থেকে বাংলাভাষা এসেছে। এই প্রাকৃত ভাষা বলতে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে লোকমুখে প্রচলিত, সংস্কৃত হতে বিবর্তিত ভাষাগুলোকে বোঝায়। বাংলাভাষা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম। এই ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন।
সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভব: সংস্কৃতভাষা হলো বাংলাভাষার আদি উৎস, যার স্বাভাবিক পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারায় বিবর্তনের অনেকগুলি স্তর অতিক্রান্ত হয়ে বাংলাভাষার জন্ম। আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাভাষার জন্ম এবং এর প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে চিহ্নিত ‘চর্যাপদ‘।
Banglar Loksanskriti Gangatikuri Gramer Shiv Gajon বাংলার লোকসংস্কৃতি গঙ্গাটিকুড়ি গ্রামের শিব গাজন
উদ্ভব থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলাভাষার ইতিহাসকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো:
১. বাংলাভাষা (প্রাচীন যুগ): সময়কাল–আনুমানিক ৯০০–১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ। নির্দশন: চর্যাপদ।
২. বাংলাভাষা (মধ্য যুগ) এই স্তরের বাংলা ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত।
(ক) আদি মধ্যস্তরের বাংলাভাষা: সময়কাল–আনুমানিক (১৩৫০–১৫০০) খ্রিস্টাব্দ। নিদর্শন: বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন‘-এর ভাষা।
(খ) অন্ত্য মধ্যস্তরের বাংলা সময়কাল–আনুমানিক (১৫০০–১৮০০) খ্রিস্টাব্দ। নিদর্শন: মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্যের ভাষা।
৩. বাংলাভাষা (আধুনিক যুগ) বা আধুনিক বাংলাভাষা সময়কাল– আনুমানিক ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ (মতান্তরে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত।
বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যে বৃহত্তর অঞ্চলে বসবাস করে তার নাম বঙ্গদেশ। কিন্তু প্রাচীন ভারতে বঙ্গদেশ বলে কোনো প্রদেশ ছিল না; ছিল কেবল বঙ্গ। যা পরবর্তীতে ‘বঙ্গদেশ‘ আখ্যা পায়। জাতি হিসেবে বাঙ্গালি অন্তত চার হাজার বছর ধরে পূর্ব ভারতে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের একটি মন্ত্র থেকে জানা যায়,
প্রজাহি তিলো অত্যায়মীয়ুর্ণান্যা অর্কমভিতো বিবিশ্রে বৃহদ্ধ তস্থৌ ভূবনেন্বন্তঃ পবমানো হরিত অ বিবেশ।
(ঋগ্বেদ ৮।১০১।১৪)
অর্থাৎ সরস্বতী সভ্যতার বৈদিক আর্যগোষ্ঠীর তিন প্রজা অতিক্রমণ করে গমন করেছিল, অন্য প্রজাগণ অর্চনী অগ্নির চতুর্দিকে আশ্রয় করেছিল এবং ভুবনমধ্যে আদিত্য মহান হয়ে অবস্থান করেছিল। বঙ্গ জাতিগোষ্ঠী প্রতীক বা টোটেম হিসেবে ‘পক্ষী‘ ব্যবহার করত। বঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র পাণ্ডু রাজার ঢিবি (আনুমানিক ২০০০ বছরের প্রাচীন) থেকে গঙ্গারিডি বা গঙ্গাহাদি সভ্যতার চন্দ্রকেতুগড় পর্যন্ত একাধিক পক্ষীমাতৃকার মূর্তি এবং পক্ষীমাতৃকার উপাসনার একাধিক নিদর্শন দেখা যায়। সর্বপ্রথম বঙ্গ শব্দটি পাওয়া যায় ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে। একশো খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে বৈদেশিক রচনায় বঙ্গের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় গ্রিকদের লেখায়। তাতে বর্ণিত আছে গাঙ্গেয় সমতল ভূমিতে বসবাসকারী গঙ্গাহৃদি নামক জাতির শৌর্য–বীর্যের কথা। স্মরণাতীতকাল হতে বাঙ্গালি জাতি পরিচয়ের ঐতিহাসিক যুগ শুরু হয়। বৈদিক যুগ, রামায়ণ–মহাভারতের যুগে রচিত নানা সাহিত্য নিদর্শনে বঙ্গভূমির উল্লেখ রয়েছে। গুপ্তরাজাদের সাম্রাজিক ছত্রছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের বঙ্গরাজ্য ও উত্তরাঞ্চলের গৌড় রাজ্য। বৃহৎ বঙ্গের প্রথম এবং ঐতিহাসিক ভাবে সুনির্দিষ্ট এবং শক্তিশালী শাসক মহারাজা শশাঙ্ক আনুমানিক (৬০০ খ্রি.-৬২৫ খ্রি.) তাঁর দক্ষ শাসনের মাধ্যমে বাঙ্গালিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর তখন থেকেই বাঙ্গালি জাতিসত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ শুরু এবং পাল ও সেন যুগে এসে সে সত্তা আরও বিকশিত হয়ে বাঙ্গালি জাতির এক শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপিত হয়। বৈদিক সাংখ্যদর্শনের রচয়িতা ও স্রষ্টা মহর্ষি কপিলের আশ্রম রয়েছে বঙ্গভূমির সাগরতীর্থে। একটি ভূখণ্ড বা বিভাগ হিসেবে ‘বঙ্গ‘ শব্দের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় পতঞ্জলির মহাভাষ্যে। পতঞ্জলি অঙ্গ, বঙ্গ, সুন্ধ এই তিনটি বিভাগ উল্লেখ করেছেন।পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ অঞ্চল সুহ্ম বিভাগের অন্তর্গত। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন নাম সুহ্ম হলেও খ্রিস্টীয় নবম–দশম শতক থেকেই সেই নাম পরিবর্তিত হয়ে রাঢ় নাম চালু হয়। প্রাচীন বঙ্গের আর একটি অর্থবহ নাম ছিল ‘গৌড়‘। বাংলা ভাষার শিকড়ে প্রাকৃত, হৃদয়ে সংস্কৃত। সেজন্যই এই ভাষায় আরবিকরণের চেষ্টা খুব একটা সহজ হয়নি। তবে বাংলার খোলনলচে পর্যন্ত পালটে ফেলার চেষ্টা চলেছে অবিরাম। ধাপে ধাপে ধ্বংস করে দেবার জন্য বারবার আক্রমণ চালানো হয়েছে। বাঙ্গালি যখন অবিভক্ত বঙ্গে সংখ্যাগুরু ছিল, প্রবল বিক্রমে সে নিজের ভাষা রক্ষা করেছে। হিন্দু বাঙ্গালি সংখ্যায় যত কমেছে, ততই বাংলার উপর জেঁকে বসেছে এক ভীষণ সঙ্কট। আরবি, ফার্সি, তুর্কি শব্দের ভারে চাপা পড়ে বাংলাভাষা ক্রমেই নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছে। তার নিজস্ব চরিত্র ম্লান হচ্ছে। কারণ প্রতিটি ভাষার কিছু নিজস্বতা থাকে। শব্দ, বাক্যের গঠন, ব্যাকরণ, উচ্চারণ, সামাজিক রীতিনীতি এইসব দিয়েই প্রত্যেক ভাষা কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে। আরব সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য হলো এর প্রতিটিকে মুছে দিয়ে ভাষাটাকে কেবলমাত্র একটা আরবের অনুসারী ভাষায় পরিণত করা। মনে রাখতে হবে, ভাষা টিকে থাকে চর্চায়। চর্চা না করলে যেমন ভাষা হারিয়ে যায়, ঠিক তেমনই যে জনগোষ্ঠী যত বেশি কোনো ভাষার চর্চা করে; সেই ভাষার উপর ওই জনগোষ্ঠী তত বেশি প্রভাব ফেলে। বাংলায় যারা কথা বলেন, তাদের মধ্যে এখন মাত্র ১৫ শতাংশ বাঙ্গালি এবং ৮৫ শতাংশ হলো বাংলাভাষী। অতএব, বাংলাভাষাতে কার প্রভাব বেশি হবে, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। আর এই ৮৫ শতাংশের প্রভাবশালী অংশের জন্যই বাংলাভাষাতে বর্তমানে আরবিকরণ চলছে। বাংলা ভাষায় এই আরবিকরণের সূচনা মূলত বহিরাগত সুফি হানাদারদের হাত ধরে। সুফিদেরকে অনেকে নিঃস্বার্থ ধর্মগুরু মনে করলেও এরা ছিলেন একাধারে যোদ্ধা ও ধর্মান্তরের কারিগর। এঁদের লক্ষ্য ছিল ছলে–বলে–কৌশলে হিন্দু বাঙ্গালিকে ধর্মান্তরিত করা। সুফিরা বাংলাভাষাকে খুব একটা সুনজরে দেখত, এমন প্রমাণ নেই। তাইবাংলা শেখার কোনো ইচ্ছা বা ধৈর্য তাদের ছিল না। তারা কথা বলত আরবি–ফার্সির মিশেল দেওয়া এক বিকৃত বাংলায়। সাতশো–আটশো বছর আগে যখন অবিভক্ত বঙ্গে সুফিদের আগমন শুরু হয়, বাঙ্গালি বলতে কেবল হিন্দু বাঙ্গালিই বোঝাত। তখনো বঙ্গে কোথাও নবাব বা সুলতানি শাসন শুরু হয়নি। ফলে সুফিদের আরবী মিশ্রিত কথা বাঙ্গালিদের পক্ষে বোঝা অত্যন্ত দুষ্কর ছিল। এমনকী ওই বিকৃত মিশ্র বাংলা সাধারণ মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল কৌতুকের বিষয়। ফলে সুফিদের ব্যবহৃত আরবি–ফার্সি–তুর্কি শব্দগুলো ঠাট্টার ছলে বাঙ্গালিরা ব্যবহার করা শুরু করে সম্পূর্ণ উলটো অর্থে।
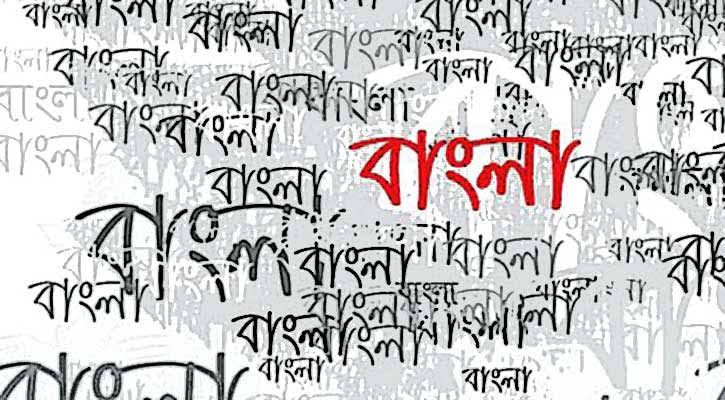
যেমন–তুর্কি ভাষায় ‘উলুগ‘ মানে হলো ‘মহান‘। এই উলুগ থেকে বাংলায় উল্লুক কথাটা এসেছে। বাংলায় উল্লুক মানে বোকা। আবার, উজবেক সেনাদের বীরত্ব গাথা সুফি পির–দরবেশদের মুখে মুখে ফিরত। কিন্তু বঙ্গবীর ইছাই ঘোষ একবার তুর্কি বাহিনী এবং তাদের উজবেক ভাড়াটে সৈন্যদলকে রাঢ়ি জঙ্গলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারার পর বাংলায় দুটো নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়। একটি হলো ‘তুর্কি নাচন‘, আরেকটি ‘উজবুক‘। উজবেক সেনাবাহিনীর কথিত বীরত্বের প্রতি বাঙ্গালির তাচ্ছিল্যের প্রতীক হলো ‘উজবুক‘! উজবুক মানে নির্বোধ। একইভাবে ‘বুজুর্গ‘ বা জ্ঞানী বৃদ্ধ বাঙ্গালির কাছে হয়ে উঠল ‘বুজরুক‘ বা ভণ্ড। সুফিদের কাছে যেটা ‘নেকি‘ বা পুণ্য, সেটাই বাঙ্গালিদের কাছে হয়ে দাঁড়াল ‘ন্যাকামি‘! আরবি জ্ঞানের ডিগ্রি ‘ফাজিল‘ বাংলা ভাষায় হয়ে গেল ফাজলামি। দুটো কথার অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। এভাবে ভাষা দিয়েই ভাষা আগ্রসনের যোগ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল বাঙ্গালীরা।
এরপরে বঙ্গের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে যখন নবাবি বা সুলতানি শাসন শুরু হল, ধীরে ধীরে আরবি অনুপ্রবেশ বিস্তার পেতে লাগল। কারণ বঙ্গে সাম্রাজ্য স্থাপন করলেও সুলতান ও নবাবদের দরবারের ভাষা বাংলা ছিল না। ফার্সি ভাষাতেই চলত বঙ্গে শাসনের কাজ। বিচারের জন্য আইন, আদালত ইত্যাদিও হত বিদেশি ভাষাতেই। ভাষা সমস্যার জন্য ন্যায়বিচার পাওয়া কার্যত ছিল অসম্ভব। যে কারণে একপেশে অযৌক্তিক বিচার–ব্যবস্থাকে এখনো বাংলাতে ‘কাজির বিচার‘ বলা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভূমি–রাজস্ব, কর আদায় ইত্যাদি সমস্ত কিছুই যেহেতু আরবি–ফার্সিতে সম্পন্ন হতো, তাই সাধারণ বাঙ্গালিকেও এসব ভাষায় কিছুটা সড়গড় হতে হয়েছিল। তারই প্রভাব বাংলা ভাষাতেও পড়ে। আইন, আদালত, জমি, দাখিল, জারি, দরখাস্ত, বরখাস্ত ইত্যাদি অসংখ্য বিদেশি শব্দ ঢুকে পড়তে থাকে সুলতানি বদান্যতায়। যেখানে বাঙ্গালি এসব বহিরাগতদের কাছে রাজত্ব হারিয়েছে, সেখানেই যোগ্য বাংলা শব্দকে ঠেলে সরিয়ে, জুড়ে বসেছে আরবি কিংবা ফার্সি শব্দ।
বঙ্গে নবাবি শাসন যখন শেষের মুখে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে ইংরেজ শাসন শুরু হতে চলেছে; তখনই গরিবুল্লা, সৈয়দ হামজা ইত্যাদির প্রেরণায় এক অদ্ভুত বাংলার আবির্ভাব ঘটে। ৩৫%-৪০% আরবি–ফার্সি শব্দ মিশ্রিত বাংলা। রেভারেন্ড জেমস লং, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ একে ‘মুসলমানি বাংলা‘ নামে অভিহিত করেছেন। ইংরেজ রাজত্বেই আরও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়, যার প্রবর্তক ছিলেন তিতুমির। বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী ছিল। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগতদের বংশধররা ছিলেন সম্ভ্রান্ত বা আশরাফ। এদের নাম কখনোই বাংলাতে হতো না।তিতুমির ছিলেন ওয়াহাবি বা শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের পুরোধা। ফলে বাংলার থেকে তার কাছে আরবি ভাষা অবশ্যই বেশি পবিত্র ছিল। আর ‘মুসলমানি বাংলা‘ ছিল, বাংলা এবং আরবির মধ্যবর্তী একটা পর্যায়। ধীরে ধীরে বাংলার থেকে আরবির দিকে যাবার একটা ধাপ। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি আমল শুরু হলে বাংলার আরবিকরণ প্রবেশ করে তার চতুর্থ থাপে। পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দু হলেও, বাংলাকেও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে জোরালো দাবি জানান ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথম দিকে মুহম্মদ শহিদুল্লাহর মত বাংলাভাষী বুদ্ধিজীবীরা একে বিশেষ পাত্তা দেননি। শহিদুল্লাহ মনে করতেন উর্দু বনাম বাংলা ঝগড়া লাগিয়ে লাভ নেই। কারণ, প্রতিটি মুসলমানের ভাষা আরবিই হওয়া উচিত। কিন্তু আরবি শিক্ষা যেহেতু উর্দুভাষী ও বাংলাভাষী, সকলের পক্ষেই খুব অসুবিধাজনক, তাই একটি নতুন সমাধান সূত্র খোঁজা শুরু হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬ সালে বাংলাকে সরকারি ভাষা করার দাবি মেনে নেয় ঠিকই। তবে সেই বাংলা সনাতন আদি বাংলা নয়। সরকারি মদতে ৩০%-৩৫% আরবি–ফার্সি শব্দ ঢুকিয়ে এক নতুন বিকৃত বাংলা তৈরি করে তাকেই মান্যতা দেওয়া হয়। খুঁজে খুঁজে বাদ দেওয়া হতে থাকে বা বিকল্প শব্দ তৈরির চেষ্টা হতে থাকে সনাতনের ছাপ থাকা যে কোন বাংলা শব্দের। ছাড় পায়নি ফুল, ফল, লতা, গাছ বা পাখির নামও। যেমন রামধনু, লক্ষ্মী মেয়ে, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, মোহনভোগ, গোবিন্দভোগ ইত্যাদি। বানিয়ে ফেলা হয় এসব বিকল্প শব্দ এবং আরবি–ফার্সি শব্দ সংবলিত নতুন বাংলা অভিধান। শুধু তাইই নয়, বাংলা লিপির বদলে আরবি লিপিতে এই নতুন বাংলা লেখা যায় কিনা, পরীক্ষা–নিরীক্ষা চলছিল তা নিয়েও।
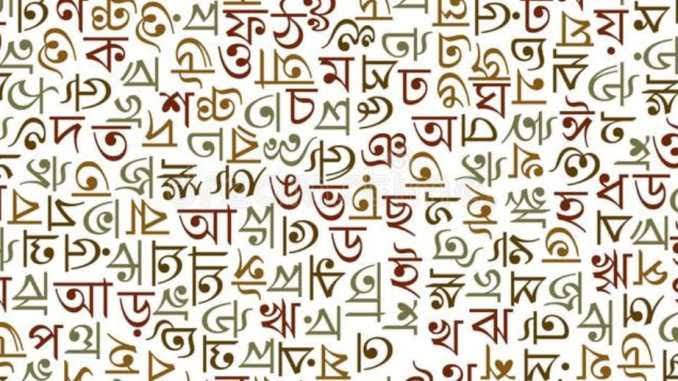
পাকিস্তান আমল শেষ হয়ে ১৯৭১ থেকে শুরু হয় বাংলাদেশ আমল। বাংলাদেশ আমলে আরবি–মিশ্রিত বাংলা তৈরির কাজে এক নতুন গতি আসে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব জুড়ে বাংলাদেশকেই বাংলা ভাষার একমাত্র ধারক–বাহক এবং বাংলাদেশের বাংলাকেই প্রকৃত বাংলা বলে প্রচার করা শুরু হয়। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটে বাংলা বলে যেটা লেখা হয় সেটা আসলে ‘মুসলমানি বাংলা‘-র বর্তমান উত্তরাধিকারী বাংলাদেশের বাংলা। বাংলাদেশের এই ভাষা সাম্রাজ্যবাদের ঢেউ এসে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার বাংলাতেও। এখানেও ধীরে ধীরে রামধনু হয়ে যাচ্ছে রংধনু, ‘লক্ষ্মী মেয়ে‘-র বদলে ভাল মেয়ের কদর বাড়ছে, বিদ্রোহকে ‘জেহাদ‘, আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। ‘চিতায় ওঠা‘-র বদলে কথ্য বাংলায় ‘কবরে যাওয়া‘ বা ‘কবর খোঁড়া‘ কথাগুলোর প্রচলন বেশি বাড়ছে। এক পা, এক পা করে বাংলা তলিয়ে যাচ্ছে আরবিকরণের অতল গহ্বরে। এই পাঁচটা ধাপ যে সবসময় একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন, তা একেবারেই নয়। কখনো দুটো বা তিনটে ধাপ পাশাপাশিই চলেছে। কখনো আবার একটা পুরোপুরি শেষ হবার আগেই আরেকটি ধাপ চালু হয়ে গেছে। কিন্তু ধাপে ধাপে আরবিকরণ ক্রমাগত এগিয়েছে। কারণ এই বিপদ সম্বন্ধে হিন্দু বাঙ্গালির সচেতনতা ছিল না। ফলে এর গুরুত্বও উপলব্ধি করা যায়নি আর সংগঠিত প্রতিরোধও করা যায়নি। আরবিকরণকে রুখতে গেলে প্রথমেই দরকার বাংলার শুদ্ধিকরণ। অর্থাৎ যোগ্য বাংলা শব্দ খুঁজে, আরবি–ফার্সি যাবতীয় বিদেশি শব্দকে বাংলা ভাষা থেকে বহিষ্কার করা। এই প্রক্রিয়াতেই সনাতন বাংলা তার নিজস্ব চরিত্র আবার ফিরে পাবে।
পল্লব মণ্ডল